নাসরিন সিরাজ এ্যানী
হৃদয় বিদারক ঘটনা হল আমার পাসপোর্টটি করতে হয়েছিল আমার সন্তানের জীবন বাঁচানোর জন্য, পর্যটনের উদ্দেশ্যে নয়। ২০০৩ সালের কথা। অতুল্য অনিমিখ, মানে আমার ছেলে, অলিন্দ ও নিলয়ের দেয়ালে ত্রুটি নিয়ে জন্মেছিল। প্রতি ১০০০ জন নবজাতকের মধ্যে এরকম ত্রুটি নিয়ে মাত্র একটি শিশুই জন্মায় বলে ডাক্তাররা আমাকে জানালো। পোড়া কপাল যে বাংলাদেশে অতুল্যের হৃদয়ের ত্রুটি ওর জন্মের বারো দিনের মাথাতেই জানা গেল কিন্তু ওকে বাঁচানোর জন্য যে ওপেন হার্ট সার্জারীটির দরকার সেটা করার মত ডাক্তার বা হাসপাতাল পাওয়া গেল না। বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিলেন অতুল্যকে নিয়ে ভারতের ব্যাঙ্গালুর শহরের এক সার্জনের কাছে যেতে। অতুল্য’র বাবা কিংবা আমার তখন টাকার এমন কোন গাছ ছিল না যেটা ঝাঁকা দিলে লাখ তিনেক টাকা ঝুর ঝুর করে পড়বে আর আমরা আমাদের অতুল্যকে নিয়ে বিদেশ যাবো, চিকিৎসার জন্য। আমরা আশা ছেড়ে দিলাম। অতুল্য’র দাদীর কথা আলাদা। তিনি ব্যপক করিৎকর্মা লোক। মাস ছয়েকের মধ্যে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে ধার করে তিনি টাকাটা ব্যবস্থা করে ফেললেন। জরুরী ভিত্তিতে আমি ও আমার ছেলে পাসপোর্ট বানালাম।
জরুরী বলে পাসপোর্টের জন্য নির্ধারিত ফিসের চেয়ে বেশী টাকা দিতে হয় সরকারকে। টাকা নিয়ে হাজির হলাম ঢাকার পাসপোর্ট অফিসের সামনে সমবেত দালালদের কাছে। না, এ গল্পের শেষ গলা কাটা পাসপোর্ট দিয়ে নয়। আমাদের জিনুইন পাসপোর্টই হয়েছিল। দালালের কাছে গিয়েছিলাম কারণ, তখন দালালের কাছেই যেতে হত। সেটাই নিয়ম ছিল। ২০০৯ সালে যখন পাসপোর্ট নবায়ন করতে আবার পাসপোর্ট অফিসে গিয়েছিলাম তখনও তাই। অবশ্য ২০১২ সালে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট করতে গিয়ে দেখি বেআইনি দালালদের হঠিয়ে সেনাবহিনী পাসপোর্ট অফিসের দখল নিয়ে নিয়েছে।
যে কথা বলছিলাম- দালালের কাজ অনেক। সে আপনার হয়ে ফরম পূরণ করবে, ছবি সত্যায়িত করার মত কাজ করবে, পুলিশ ভেরিফিকেশনের কাজ সামলাবে, সব শেষে পাসপোর্ট ডেলিভারী নিয়ে আপনাকে কল করবে। পাসপোর্ট অফিসের বিভিন্ন টেবিলে টেবিলে আপনার নিজের ঘুরতে হবে না, দালাল আপনার হয়ে ঘুরে দেবে। আমার দালালটি সৎ লোক ছিল। সততার প্রমাণ দিতে সে পাসপোর্টের ফি’র টাকাটা নিল না; আমার টাকা আমিই ব্যাংকে জমা দিলাম।
দালালের সাথে আমার গোল বাঁধলো পাসপোর্টের স্থায়ী ও অস্থায়ী ঠিকানার জায়গাটি পূরণ করতে গিয়ে। দালালের উৎকন্ঠা আমি আমার সত্যিকারের ঠিকানা লিখলে পুলিশ সেটা সত্যি সত্যি ভেরিফাই করতে যাবে যার ফলে আমাকে হেনস্তা হতে হবে। সম্ভবতঃ তাঁর কিছু চেনা পুলিশ আছে। ঐ ঠিকানাগুলো হয়তো ভুয়া না। কিন্তু পরিচিত পুলিশ বলে ভেরিফিকেশনের সময় হয়তো “ফাঁকিটা” খাতায় লেখা হয় না। পত্রিকায় খেয়াল করেছি ঠিকানা মিলছেনা এমন মৃতদেহের বিজ্ঞাপন দেয় সরকার। বেওয়ারিশ লাশ হতে চাই না আমি তাই পাসপোর্টে কোন মিথ্যা তথ্য বা ঠিকানা দিতে রাজী হলাম না। পুলিশ ভেরিফিকেশনকে আমি ভয় পাই না, কারণ আমার কোন ক্রিমিনাল রেকর্ড নেই। পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য পাসপোর্ট পেতে দেরী হবে বলে ভয় দেখালো দালাল। তাতেও আমি সত্য বলতে পিছু হঠি না। শেষ পর্যন্ত আমার সত্যিকার ঠিকানা পাসপোর্টের ফরমে লিখে দালালের হাতে কাগজপত্র বুঝিয়ে আমি বাড়ি ফিরে এলাম। কিন্তু দালালের কথা না শুনে আমার বাড়ির আসল ঠিকানা পাসপোর্টের ফরমে লেখায় পুলিশ ভেরিফিকেশন নামে আমাকে যে অপমান ও নাজেহালের শিকার হতে হয়েছিল সেই অভিজ্ঞতা নিয়েই আজকের গল্প। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নীতি বানানেওয়ালারা যে এই সমাজ সম্পর্কে তিল পরিমাণ বাস্তব ধারণা রাখেনা, উল্টো কতগুলো মনগড়া ধ্যান ধারনা নিয়ে পরিচালিত হয় এসবই পাঠকের জানা আছে। আরো জানা আছে যে এই জাতি রাষ্ট্রের সীমানার স্বনিয়োজিত শাসক হয়ে এই মানুষগুলো আমাদের মত আমজনতাকে মানুষ হিসেবে সম্মান না দেয়ার চর্চা চালিয়ে যায়। আজকের গল্পে সেই জানা গল্পই আবার বলবো।
পুলিশ যখন ভেরিফিকেশন করতে আসলো সে সময়টা ছিল বিকালবেলা। আগস্ট মাস ছিল তখন। সে বছর ভীষণ গরম পড়েছিল। তার উপর আমাদের বাসা ছিল ঢাকা শহরের ঘনবসতিপূর্ণ এক এলাকায়, ছয়তলা ভবনের টপ ফ্লোরে। এলাকাটিতে গাছপালা বলতে প্রায় কিস্যু নেই। আছে শুধু গায়ে গা লাগানো ছয় তলা ভবনের সারি। হঠাৎ হঠাৎ দু’একটা প্লট খালি দেখা যায় বটে। সেখানে ছোট/বড় ছেলেরা (মেয়েরা নয়) মৌসূম অনুযায়ী ক্রিকেট বা ব্যাডমিন্টন খেলে। তাও দুই মৌসূম ঠিকমত খেলতে পারে, কি পারে না। খালি জায়গাটা দখল করে নেয় আরেকটা বহুতল ভবন। এলাকায় সবুজ বলতে দু’একটা ছাদে বড় বড় টবে মাটি ভরে মধ্যবয়সী বাড়িওয়ালা/বাড়িওয়ালীদের তৈরী করা বাগানগুলো। সারাদিন ধরে রৌদ্রে জ্বলা কংক্রিটের দেয়াল থেকে যে তাপ বের হচ্ছিল তার সাথে আকাশের গোধূলীর লালচে আলোটা বেশ মানিয়ে গিয়েছিল। বাসায় ইলেকট্রিসিটিও ছিল না। মনে হচ্ছিল যেন তন্দুর রুটির বড় সড় একটা চুলার ভেতরে আমরা সবাই বসে আছি। বাড়িটা সেদিন জমজমাটই ছিল। পাশের পাড়া থেকে অতূল্য’র দাদী তাঁর কুয়েত প্রবাসী ভাবীকে নিয়ে নাতিন দেখতে এসেছেন। অতুল্য বেশীদিন বাঁচবেনা সবাই মনে মনে সেটা আশংকা করছিল কিন্তু কারো মুখে কোন হতাশাব্যঞ্জক ভাষা বা ইঙ্গিত নেই। মামী স্বর্ণের হার উপহার এনছেন অতুল্য’র জন্য। স্তন থেকে টেনে টেনে দুধ খেলে অতুল্য’র হার্ট ও লাংসে চাপ বাড়ে তাই ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী আমি একটা বাটিতে আমার স্তনের দুধ বের করে অতুল্যকে চামচ দিয়ে খাওয়াচ্ছিলাম। অতুল্য’র বাবা শোবার ঘরে বিছানায় গড়াচ্ছিল।
পুলিশের সাথে আমার এনকাউন্টার খুব কমই হয়েছে। তবে যতবার হয়েছে প্রতিবারই আমার যেটা উপলব্ধি হয়েছে তা হল: পুলিশরা মেয়েদের “যৌন ক্রিমিনাল”হিসেবেই প্রথমে সন্দেহ করে। হয়তো এটাই তাদের কারিকুলামের প্রশিক্ষণ। কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে আমার উপলব্ধির ভিত্তিটা ব্যাখ্যা করছি।
প্রথম অভিজ্ঞতা ধানমন্ডির লেকের পাড়ে। দিনটা ছিল পয়লা ফাল্গুন। ১৯৯৪ সাল। তখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। ক্লাশের বন্ধুদের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পয়লা ফাল্গুন উৎযাপন সেরে বাড়ি ফেরার পথে পার্কের সবুজ ঘাস দেখে সেখানে একটু বসার লোভ সামলাতে না পারাতেই বিপত্তিটা ঘটে। আমার সাথে আমাদের ক্লাশেরই আরেক ছেলে ছিল। আমাদের দু’জনের বাসা ধানমন্ডি এলাকায় ছিল বলে একসাথে ফিরছিলাম আমরা। ছেলেটির খুব বেশী আগ্রহ ছিল না পার্কে বসার জন্য। আর আমার জানা ছিল ছেলেটা সাথে আছে বলেই এখন পার্কে বসা যাবে; বাংলাদেশে একা একটা মেয়ের পার্কে বসাটা “খুবই অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক” পার্কে বসেই পায়ের পাতা দিয়ে ঘাসগুলো অনুভব করছিলাম আমি আর আমার ক্লাশমেট লাজুক হেসে বলেছিল, “তোমার পা টা খুব সুন্দর”।
না, প্রেম করছিলাম না আমরা। বরং, পার্ক থেকে আমাদের দ্রুত চলে যেতে হবে সেটাই ছিল আমাদের আলাপের মূল প্রসঙ্গ। নিজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করে আমার বন্ধুটি: একবার সে তার প্রেমিকার সাথে এই পার্কে বসেছিল। রাস্তা দিয়ে একটা পুশিলভ্যান যাচ্ছিল। ওদের বসে থাকতে দেখে ভ্যানটা থামে এবং পুলিশ ওদের ডেকে নিয়ে “খুব খারাপ আচরণ করে” আচরণটা এতোই খারাপ ছিল যে ওর প্রেমিকা সেদিন অপমানে কেঁদে ফেলেছিল। ওর ভাষ্যমতে পুলিশগুলো নাকি ইঙ্গিত করছিল যে ওর প্রেমিকা “ভদ্র ঘরের মেয়ে না” ওরা তাদেরকে থানায় নিয়ে যাবার হুমকিও দিচ্ছিল। পুরোটা সময় নাকি পুলিশ ছেলেটির সাথেই কথা বলছিল, মেয়েটির সাথে না। আমার বন্ধু ব্যাখ্যা করছিল যে ঐদিন তার মেয়েবন্ধুটি সাথে থাকাতেই পুলিশ তাকে নাজেহাল করেছিল। নাজেহালের মাত্রা বাড়ার কারণ, আমার বন্ধুটির ব্যাখ্যায়, সময়টা ছিল সন্ধ্যা আর পুলিশ আসার সাথে সাথে “আমরা এখুনি চলে যাচ্ছি” না বলে উল্টো ও পুলিশের সাথে ও তর্ক করছিল। পুলিশকে উল্টো প্রশ্ন করছিল, “কেন একটা ছেলে একটা মেয়ে পার্কে এক সাথে বসতে পারবে না?”; “আমরা তো এখানে ‘আপত্তিকর’ কিছুই করছি না”।
আমার ক্লাশমেটের গল্প বলা শেষ হয়েছে কি হয়নি এরই মধ্যে আমরা দেখতে পেলাম একটা পুলিশ ভ্যান রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে কিছুদূর গিয়ে থেমে গেল। আমাদের অনুমান সত্য প্রমাণ করে পুলিশ ভ্যান থেকে নামলো একজন কম পদমর্যাদার পুলিশ এবং সে আমাদের দিকে হেঁটে আসতে থাকলো। বাড়ি ফেরার তাড়া ছিল বলে আমরা এমনিতেই রাস্তা থেকে বেশী দূরে বসিনি। আর তাছাড়া আমার বন্ধুর অভিজ্ঞতা শোনার পর আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করারও প্রয়োজন পড়লো না যে আমরা পুলিশের সাথে তর্ক না করে এখন সোজা বাড়ি চলে যাবো। উচ্চ পদমর্যাদার পুলিশের ডাকে সাড়া দিতে আমরা তাই নীচু পদমর্যাদার পুলিশের পিছু পিছু পুলিশ ভ্যানের কাছে গেলাম। এবং পুলিশের পক্ষ থেকে করা সাধারণ জেরা ও উপদেশগুলো , যেমন: “এখানে আপনারা কি করছেন”, “আপনাদের বাসা কোথায়”, “গল্প করতে হলে বাসায় ড্রইং রুমে বসে করেন” নিয়ে ন্যায্য তর্ক করা থেকে বিরত থাকলাম। বিনা বাক্য ব্যয়ে পুলিশের সাথে আমার প্রথম এনকাউন্টার পার হল। পুলিশের ভাবটা এরকম – মেয়েদের পার্কে বসাটাই অপরাধ। এই মেয়েটির পার্কে বসার প্রথম কারণ হতে পারে যে মেয়েটি দেহব্যবসা করে।
দ্বিতীয় ঘটনাটি আরো চমকপ্রদ। ঘটনাটি ঘটে ধানমন্ডিতে অবস্থিত জার্মান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র- এর সামনে। সম্ভবতঃ সেটা ২০০১ সাল। সেদিন আমি আর অতুল্য’র বাবা সেখানে গিয়েছিলাম সিনেমা দেখতে। তখনও আমরা দু’জন একসাথে সংসার করতে শুরু করিনি। আমাদের সাথে অতুল্য’র বাবার একজন ছেলে ও একজন মেয়ে বন্ধু ছিল। সেদিন কি ছবি দেখেছিলাম সেটা এখন আর মনে নেই। এটা মনে আছে যে ছবি দেখা শেষ করে আমরা চারজনই নিজেদের মধ্যে ছবির ভাল মন্দ নিয়ে ক্যাচর ম্যাচর করছিলাম। কেন্দ্রের গেইটের ঠিক বিপরীতেই ছিল একটা খুপরী চায়ের দোকান। দোকানটা আসলে ধানমন্ডি আট নম্বর মাঠের ভেতরেই ছিল কিন্তু মুখটা কেন্দ্রের দিকে ঘোরানো। ফলে কেন্দ্রে সিনেমা দেখতে আসা লোকজন মাঠের সীমানা প্রাচীরের গ্রীলের ফোঁকরে হাত গলিয়ে দোকানদারের কাছ থেকে চা-বিড়ি কিনে সেগুলো সহযোগে ঐখানেই ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়ে বা বসে দিব্যি আড্ডা দিত। সেদিনও অনেকেই আড্ডা দিচ্ছিল। আমরাও । হঠাৎ আমাদের চোখ ধাঁধিঁয়ে পুলিশের একটা টহলরত ভ্যান ঘ্যাচ করে আমাদের সামনে থামলো, ড্রাইভারের পাশে যে পুলিশটি বসে ছিল (সাধারণতঃ উচ্চপদস্থরা এই সীটে বসে) সে দরজা খুলে নেমে আমাদের দিকে ছুটে আসলো। সে চিৎকার করছিল: “তোরা এখানে কি করস!”, “ঐ তুই ভ্যানে ওঠ।”, “তোগোরে এখনই থানায় নিয়া যামু।”
পাঠক বিশ্বাস করুন তাদের ভঙ্গী ও মুখের ভাষা নিয়ে আমি একটুও বানিয়ে বলছি না। আমাদের অপরাধ বুঝতে সংবিধান বা আইনের বইপত্র আপনাকে সাহায্য করতে পারবে না, আশ্রয় নিতে হবে “অসামাজিক কার্যকলাপ” নামের এক অস্পষ্ট ধারণার। আপনি বাংলাদেশে আমার সময়ে বেড়ে উঠে থাকলে এই অস্পষ্ট ধারণাটি অন্তর্জ্ঞান দিয়ে এরই মধ্যে বুঝে গেছেন। সেই অনুযায়ী, আমাদের অপরাধ আমরা ছেলে-মেয়ে একসাথে ঘনিষ্ঠভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন ফুটপাথে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম। আমাদের আরো অপরাধ আমরা ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে ধুমপান করছিলাম। সম্ভবত: আমাদের সবচাইতে বড় অপরাধটি ছিল আমরা “প্রেম” করছিলাম। মানে, ২০-২৫ বছর বয়সী ছেলে মেয়েরা যা করে আর কি, এই যেমন, কারনে অকারনে হেসে খুন হয়ে ছেলে বন্ধুদের গায়ে মেয়েদের হেলে পড়া, হাসতে হাসতে মেয়ে বন্ধুর মুখের উপর এসে পড়া চুল ছেলেটির সরিয়ে দেয়া, কিংবা বেশী সাহসী হয়ে পাবলিকলিই টুক করে ছোট একটা চুমু খাওয়া। প্রচলিত আইনে এগুলো অবশ্য অপরাধ না, এমনকি আচরণগুলো খুব বিরলও না। সাধারণ লোকজন এ নিয়ে খুব যে মারমুখী তা ও না। কেউ হয়তো বিরক্ত হয়ে এদের নির্লজ্জ বলে, কেউ ছেলেমানুষ। কেউ হয়তো এসব দেখেও না দেখার ভান করে আবার কেউ হয়তো নস্টালজিক হয়ে পড়ে। তবে বাংলাদেশের পুলিশের ব্যপার আলাদা। তারা তাদের চাকরি ও উর্দির ক্ষমতার জোরে “অসামাজিক কার্যকলাপ” বন্ধে তৎপর হয়ে উঠতে পারে।
আমার মনে আছে ঐদিন আমরা উল্টো ব্যাপক হৈ চৈ করেছিলাম পুলিশের সাথে। ততদিনে আমরা সাংবাদিকতা পেশার সাথে জড়িয়ে পড়েছি। সেই সুবাদে আমরা জানি যে সাংবাদিকদের সাথে পুলিশরা তেড়িবেড়ি করে না। তাছাড়া জার্মান সংস্কৃতি কেন্দ্রের দারোয়ানও স্বাক্ষ্য দিল যে আমরা এখানকার নিয়মিত দর্শনার্থী। তার মানে আমরা ক্লীন। পুলিশ আমাদের ভ্যানে তুললো না। পুলিশ চলে যাবার সময় উপরন্তু আমরা বলতে থাকলাম “আপনি যে আমাদের তুই তোকারি করেছেন তার জন্য ক্ষমা চান”।
আমার মত এরকম অনেক অনেক অভিজ্ঞতা সকলের দৈনন্দিন জীবনে আছে যেখানে পুলিশের আচরণ দেখলে মনে হয় আমরা, নারীরা, সব দেহ ব্যবসার সাথে জড়িত আর পুলিশ যেন আমাদের সাথে যাচ্ছেতাই আচরণ করার এমনকি ভোগ করারও আইনি অধিকার রাখে। এরকম একটা পরিস্থিতিতে পাসপোর্টের আবেদনের ভেরিফিকেশনের কাজে যখন পুলিশটি আমাদের বাসায় ঢুকলো তখন আমাদের তিনজনেরই অতুল্য’র জন্য উৎকন্ঠার পাশাপাশি নিজেদের “নারী” অস্তিত্ব নিয়ে একপ্রকার অস্বস্তি তৈরী হল। পুলিশটি চলে যাবার পরে আমার চাচি শ্বাশুড়ি বলেছিলেন যে পুলিশটি তার বুকের দিকে, গলার সোনার হারের দিকে বার বার তাকাচ্ছিল আর তিনি অস্বস্তিতে ওড়না টেনে নিজেকে আরো ঢাকতে বাধ্য হয়েছিলেন।
ভেরিফিকেশনের নামে পুলিশটি যা করলেন সেই কথায় আসি। প্রথমেই তিনি আমার স্বামীর তলব করলেন এবং তাকে দিয়ে একটি চিঠি লেখালেন যে আমি আমার স্বামীর স্ত্রী এবং আমার বিদেশ ভ্রমনে আমার স্বামীর কোন আপত্তি নেই। নারীকে সমমর্যাদার নাগরিক হিসেবে সম্মান করায় যে তাদের সমস্যা আছে তার প্রমাণ বরাবরই পুলিশরা আমাকে দেখিয়েছে কিন্তু এই আচরণটি আমার কল্পনারও বাইরে ছিল। পাসপোর্ট আমার নিজের, দেশের বাইরে যাবো আমি নিজে আর রাষ্ট্র তার সীমা অতিক্রম করতে দরকারি এই বইটি আমাকে দিচ্ছে তার একজন নাগরিক হিসেবে। এখানে আমি কার স্ত্রী এটা কিভাবে প্রাসংগিক? প্রাসংগিক, কারণ প্রায়শই যা হয় আর কি- নারীও যে মানুষ সেটা রাষ্ট্র পরিচালনাকারী মানুষদের কিছুতেই মাথায় ঢোকে না। কিংবা হয়তো মনে হয় নারী এমন এক মানুষ যার “নিরাপত্তা” নিশ্চিত করতে সব সময় স্বামী অথবা পুলিশ দরকার। তাই তারা নিজেরা নিজেরা একটা কাল্পনিক জোট তৈরী করে। যাই হোক, আমি পুলিশটিকে প্রশ্ন না করে পারলাম না। উত্তরে আমাকে পুলিশটি বললেন, “ এটা আপনাদের ভালো’র জন্য করা হইসে। নারী পাচার ঠেকানোর জন্য”

আলোকবাজি: লেখক
উত্তর শুনে আমি পুরা তাজ্জব বনে যাই। কারণ, নারী পাচার নিয়ে যে সব তথ্য জানা যায় তাতে দেখা যায় বিয়ের মাধ্যমেই নারী পাচারের সিংহভাগ ঘটনা ঘটে থাকে। আর পুলিশের ভূমিকাও এখানে পাচারের সহযোগি হিসেবেই দেখা যায়। তবে, এ নিয়ে আর কথা বাড়ালাম না, কারণ পাসপোর্টটি আমার দরকার। ভেরিফিকেশনের কাজ শেষ করে যাওয়ার আগে পুলিশটি ২০০ টাকা দাবী করে বসলো। এটা নাকি তার আমার বাড়ি বয়ে এসে জরুরী রাষ্ট্রীয় কাজ সম্পাদনের জন্য একটা বখশিশ মাত্র। সরকার যে বেতন দেয় তাতে যে তাদের মোটর সাইকেলের পেট্রোলের খরচ ওঠেনা এই সব নানান কথা বার্তা ২০০ টাকা পকেটস্থ হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি চালিয়ে গেলেন।

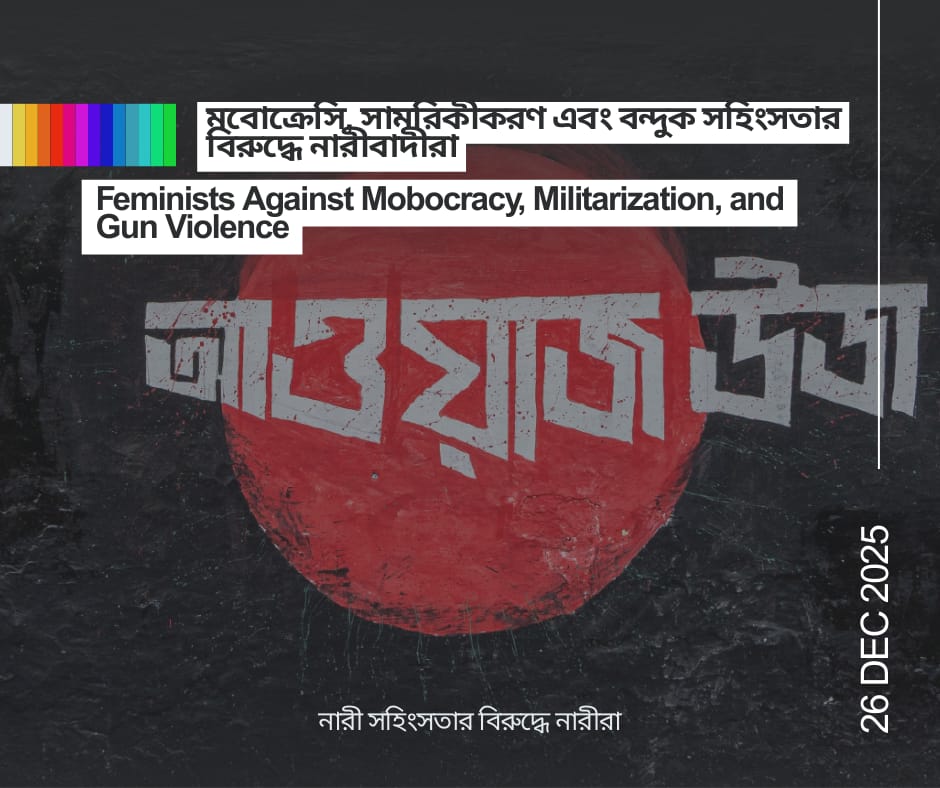
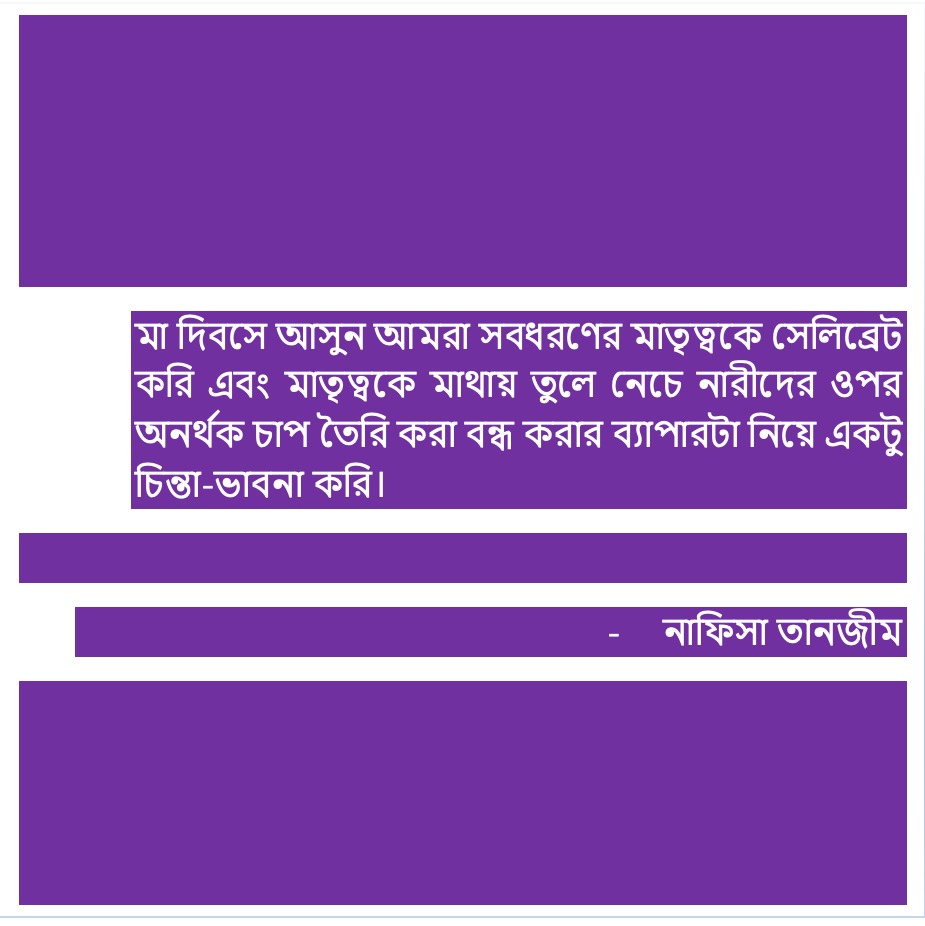
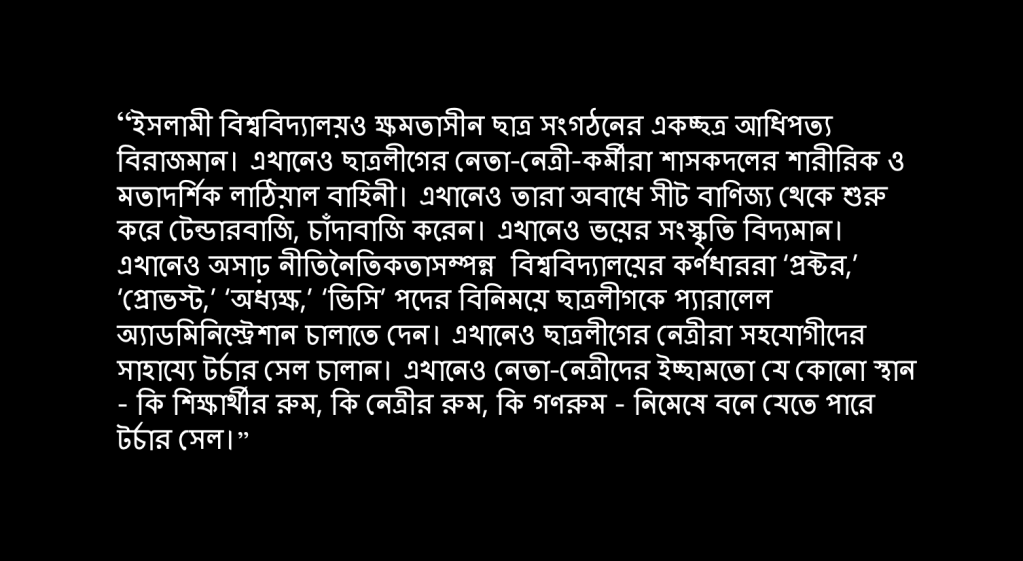

Leave a comment