লেখাটি চাঁদপুর জেলার এক গহীন গ্রামের একজন মুক্তিযোদ্ধার সাথে ধারাবাহিক আলাপচারিতার (২০১১-২০১২) ভিত্তিতে তৈরী করা হয়েছে। তাঁকে পাড়ার সবাই মুক্তিযোদ্ধা কাকা ডাকেন, আমিও তাই ডাকতাম। তাঁর পরিবারের সাথে সামাজিক সখ্যতা গড়ে উঠেছিল, ওই অঞ্চলে তারাই ছিলেন আমার পরম আত্মীয়। ওনার প্রতিটা কথা মনে হত উধ্বৃতি আকারে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখি। সামাজিক সম্পর্কের পরিসরে আলাপ-আলোচনা কখনো রেকর্ড করা হয়নি। কিন্তু আমি ডায়েরি খুলে খুলে লিখে রাখতাম। তাই নিয়ে খুব হাসা-হাসিও ছিল। অনেক সময় বকাও দিয়েছেন কাকা, কথার মাঝখানে উঠে আমি গিয়েছি ডায়েরির খোঁজে! সেই ডায়েরি-র পাতা থেকে স্বাধীনতা, সাম্প্রদায়িকতা ও দেশপ্রেম নিয়ে তাঁর ভাবনাগুলোকে এখানে রিকন্সট্রাক্ট করেছি। ইচ্ছে করেই কিছু ডিটেল উল্লেখ করি নাই, ছদ্ম নাম ব্যবহার করেছি।
১
আজ কয়েক দিন হল মুক্তিযোদ্ধা কাকার কথাই ভাবছি। রোজ মনোযোগ দিয়ে কয়েকটা খবরের কাগজ পড়তেন। মাঝে মাঝে জরুরি খবর কেটে ঘরের দেয়ালে সেটে রাখতেন।
কাকার তোষকের নিচে ছিল এক অনন্য নিউজ পেপার আর্কইভ। বিছানাটা দেয়ালের সাথে লাগানো। খাটের তিন কোণায় ছিল কাকার জীবনের তিনটি ভিন্ন সময়কালের জমানো খবরের কাগজ। দেয়াল ঘেঁষা খাটের বা-দিকের কোণায় ’৭২-এ দেশে ফেরার পর থেকে ’৭৩ পর্যন্ত খবর; ডান দিকে পায়ের কাছে ’৮৩-এ অসুস্থ হয়ে কিছুদিন গ্রামে এসে থেকেছিলেন, সেই এরশাদ আমলের খবর; আর মাথার কাছে হল সাম্প্রতিক খবর, চট্টগ্রাম সেনানিবাসের চাকরি থেকে অবসর নিয়ে যখন (২০০৭) একবারে দেশের বাড়ি চলে আসলেন তারপরের খবরাখবর। কাকার ভাণ্ডারে চাঁদপুরের স্থানীয় পত্রিকারও কাটিং ছিল।
কথায় কথায় মাথা নেড়ে বলতেন, ইতিহাসের হিসেব রাখাটা খুব জরুরী।
২
তাঁর সাথে প্রথম দেখা ২৫শে মার্চ রাতে। ২০১১ সাল। কাজে চাঁদপুরে এসেছি। যে বন্ধু আমাকে শহরের পথ-ঘাট চেনালেন, তিনিই আমাকে কাকার বাড়িতে থাকার ব্যাবস্থা করে দিলেন। রোজদিনের মতন সেদিনও বিদ্যুৎ নেই। হারিকেনের আলোয় গল্প শুনছি। বাড়ির অন্যদের কাকার গল্প শোনার তেমন আগ্রহ নেই। কাকী আমাদের বসিয়ে বড় জা’র ঘরে গেছেন। তমা আর তমাল – মোবাইল নিয়ে খেলছে, বাবার গল্পে ওদের কান নেই। সেই রাতের কথা তারা বহুবার শুনেছে। আমি আসাতে ওদের ভালই হয়েছে।
অনেক রাত পর্যন্ত জেগে কাকার মুখে শুনলাম সেই উত্তাল মার্চের কথা । তখন তিনি চট্টগ্রাম সেনানিবাসে কর্মরত ছিলেন। নিরস্ত্র মানুষের উপর পাকহানাদার বাহিনী যখন আক্রমণ করল, আরও অনেক বিদ্রোহী সেনা সদস্যদের সাথে তিনিও পথে নামলেন। পায়ে গুলি খেয়ে গড়িয়ে পড়ে গেলেন এক ডোবাতে। পচা-গলা পানিতে আহত, চেতন-অচেতন পড়ে ছিলেন। ভাগ্যক্রমে তিনদিন পর সেনাবাহিনীরই এক কর্মচারী পানিতে নড়াচড়া দেখতে পেয়ে ডোবার কাছে যায়, এবং কাকাকে চিনতে পারেন। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু তিনদিনে রক্তক্ষরণ হয়েছে প্রচুর। ময়লা পানিতে পায়ের ক্ষতস্থানে দগদগে ঘা। অর্ধচেতন কাকা টের পেলেন তিনি গ্রেপ্তার হয়েছেন। চিকিৎসার জন্য তাকে সামরিক বাহিনীর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। জান বাঁচাতে কাকার একটা পা হাটুর খানিকটা উপর হতে কেটে ফেলা হল। পুরোপুরি সেরে ওঠার আগেই পাকিস্তানের একটি জেলখানায় তাকে স্থানান্তর করা হয়েছিল।
পশ্চিম পাকিস্তানের জেল জীবন নিয়ে কাকার গল্পগুলো খুব মজার। টুকরো টুকরো, অসম্পূর্ণ। জেল খানায় বসে তিনি পাঠানি কুর্তা আর সালোয়ার বানানো শিখেছিলেন। এক জেলর তাকে একটা সিঙ্গার মেশিনও কিনে দিয়েছিলন। রীতিমতন সেলাই করে আয় করতেন। যুদ্ধ শেষে এক হাতে ক্রাচ আর অন্য হাতে সেই সিঙ্গার সেলাই মেশিন নিয়ে তিনি দেশে ফিরলেন।
কাকার মৃত্যুর পরে (১৯ নভেম্বর, ২০১২) তমা বাড়ির এক কোনায় সেলাই মেশিন, ক্রাচ আর কাকার প্রস্থেটিক লেগটা সাজিয়ে রেখেছে। কৃত্রিম পায়ের সাথে জুতামোজাও সাজানো আছে।
৩
অন্য একটা কারণে কাকার কথা মনে পরছে গত কদিন।
দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে যুদ্ধবন্দীদের সাথে দেশে ফিরলেন। একটা পা নেই। নতুন করে জীবনকে বুঝে নিতে হবে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তখন নানাভাবে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। কাকারও সেনাবাহিনীতে মর্যাদাসম্পন্ন কাজের সুযোগ হল। তবে কাজটা পেতে তাকে বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হল। এ সময়টা তিনি চাঁদপুরে নিজ গ্রামে চলে আসলেন।
সেই সময়ের কথা কাকার কাছে শুনলাম একদিন।
’৭২-এ গ্রামে ফিরে এসে আমি যা দেখেছি, সে সময়ের চিহ্ন আমার শরীরে আছে। অরাজকতা আর অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়েই শুরু হল স্বাধীন দেশে আমাদের জীবন। হিন্দু ভাইবোনদের জন্য এই অনিশ্চয়তা ছিল অন্য রকম। একদিকে প্রতিবেশীর হয়রানি। কেউ উঠানে রোদে শুকাতে দেয়া হলুদগুড়াতে বালু মেশায়, বা কেউবা মরিচ চুরি করে, আবার কেউ আম গাছের ডাল কেটে ঘরের উঠানেই ফেলে যায়। অন্যদিকে ছিল সরকারি নজর। এলাকার নতুন স্কুল হবে, সাবার আগে অধিগ্রহনের শিকার হবে গ্রামের হিন্দু পরিবারের কৃষি জমি। নানা কিছু করে হিন্দু ভাই-বোনদের এলাকা ছাড়া করার চেষ্টা। যুদ্ধ ফেরত মুক্তিযোদ্ধারা সকলে কিন্তু সাথে সাথে অস্ত্র ফেরত দিল না। বীরের উপাধিতে অনেকের রক্ত গরম, ন্যায়-অন্যায় নিয়ে মাথা ঘামায় নাই। এমন অরাজকতার সময়ে আমরা কয়েকজন রাতে পাড়া পাহারা দিতাম।
এক রাতে আমার উপর হামলা হল। পেছন থেকে ছুরি দিয়ে আক্রমণ করল। এত্ত বড় ছুরি। আমার ডানার কাছ দিয়ে ঢুকে সামনে দিয়ে বের হইল। তখন এখানে হাসপাতাল ছিল না। সেই কুমিল্লা থেকে এক ডাক্তার আনতে গেল। রক্ত বন্ধ করার জন্য কত কি? কেউ বলে চুন দিতে, কেউ চিনি ঢালল তো কেউ ভিনেগার। কোথায় কোন বাজারে গেছে ভিনেগার খুজতে। ডাক্তার আসার আগেই অবশ্য তোমার আনিস চাচা হ্যাচকা টান দিয়ে ছুরি বের করে ফেলল। তারপরে কত দিন এই বিছানায় শোয়া।
আমি খানিকটা উত্তেজিত হয়েই বললাম, আপনি একজন মুক্তিযোদ্ধা, আপনার উপর হামলা হল! এই নিয়ে কি হুলুস্থুল পড়ে গেল?
কাকা হেসে বলল, গ্রামের মুক্তিযোদ্ধাদের তখন তেমন খোঁজ-খবর ছিল না, ঢাকাতেই চলছিল যত মালা দেয়া নেয়া। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমার নিয়মিত যাতায়াত শুরু হয় আরো অনেক পরে। ধরো ‘৯০ দশকে। তার আগ পর্যন্ত কর্মস্থলে সকলে জানত আমি মুক্তিযোদ্ধা, ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় কর্মসূচিতে গিয়েছি মাঝে মধ্যে, কিন্তু নিয়মিত আনুষ্ঠানিকতা আরো অনেক পরের ঘটনা।
এখন যে কৃত্রিম পা দেখছো, এটাতো ছিল না তখন। ক্রাচে ভর করে পার করেছি জীবনের একটা বড় সময়। তখন এসব ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন টিশনও ছিল না, মানবাধিকার আন্দোলনতো আরো পরে শুরু হইসে। যাইহোক, এই যে সদ্য স্বাধীন দেশে হিন্দু পরিবারগুলো রোজ দিন যে অনাচার সহ্য করলো, আবার কেউ করলো না, দেশ ছাড়লো — সেটাই কিন্তু এই দেশে কি চলবে আর চলবে না তার মান ঠিক করলো।
চারিদিকে তখন কত হতাশা। আবার একই সঙ্গে প্রলোভন। একটি যুদ্ধবিধ্বস্থ নতুন দেশ। যতদিন গেল, লক্ষ্য করলাম, জায়গা-জমি স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু দেশগড়ার যুদ্ধে কেউ যোগ দিতে চায় না!
রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে কাকী আমাকে ইশারা করল, কাকার হার্টের সমস্যা আছে, বেশি উত্তেজিত হওয়া বারণ, কথার মাঝখানেই আমি বিদায় নিয়ে চলে আসলাম।
কাকা বিদায় দিতে গিয়ে বললেন, আরেকদিন তোমার আনিস চাচাসহ আলাপ হবে। ’৭২ আমার ওপর হামলার সময় উনি সাথে ছিলেন। উনিও বলবেন তোমাকে, দেশটাকে গড়ে তোলার সংগ্রামে কেউ শামিল হল না।
কিন্তু কেন? দু’দিন আগেইতো এই দেশের মানুষ দেশের জন্য মরতে প্রস্তুত ছিল।
৪
শেষ যেদিন মুক্তিযোদ্ধা কাকার সাথে দেখা হল। সেদিনের কথাগুলো এখনও আমার কানে লেগে আছে। আমরা সবাই চা নিয়ে গল্প করছি। খুব গরম ছিল সেদিন। হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেল। সরকারের কুইকরেন্টাল প্রকল্পগুলো নিয়ে কথা বলতে গিয়ে, কাকা আবার সেই দেশগড়ার যুদ্ধের কথা তুললেন। তিনি বললেন, কুইকরেন্টাল প্রকল্পগুলোতে কিভাবে দুনীর্তি হচ্ছে এতসব সূক্ষ মারপ্যাচ আমি বুঝি না। একজন মুক্তিযোদ্ধার দায়িত্ব স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা ওড়ানোতেই শেষ নয়।
কাকা খুব হেসে হেসে বলত, এই দেশগড়ার যুদ্ধে কেউ শরীক হতে চায় না।
শোকে অস্থির কাকী আমাকে বুঝিয়ে বলেন, তোমার কাকা মাসের শেষে মারা গেল। এখন আর কুলখানি কিছু করব না। আগামী শুক্রবার যারা দোআ কালাম পড়ছে, গোছল দিছে, কবর খুড়ছে, কোরবানীর মাংস আছে, তাই দিয়ে তাদের খাওয়াব। মাসের প্রথমে পেনশনের টাকা উঠাব, তারপরে মিলাদ হবে, লোক খাওয়াব।
কাকার অনুপস্থিতিতে অলস পড়ে আছে চশমা, লাঠি, জুতা, শীতের সোয়েটার। ঘর জুড়ে তাঁর গমগমে কণ্ঠস্বরের অভাব। তারমধ্যে কাকীর পাশে বসেছিলাম। নীরব অনুপস্থিতিতেই কাকার চিন্তা, দর্শন আমার মনে অনুরনিত হল। কাকা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, দেশের মুক্তি কেবল ভুখন্ডে দখল প্রতিষ্ঠায় সীমিত নয়। তিনি বলতেন, দেশের জনগণ স্বাধীন ভূখন্ডের আত্মা। এই জনগণের সৎ ও সাহসী সুনাগরিক হয়ে ওঠার মধ্যদিয়েই দেশের আত্মার মুক্তি, প্রকৃত স্বাধীনতা।
একদিন আনিস চাচার সাথে কি নিয়ে যেন তুমুল তর্ক লেগে গেল। চিৎকার শুনে আমরা দৌড়ে বৈঠকখানায় চলে আসলাম। কাকা হুংকার দিয়ে বললেন, মুক্তিযোদ্ধাকে দেবতা বানালো কে? যত্তসব।
কাকার সাফ কথা, সেদিন যিনি মহান ছিল, আজ যদি সে চোর হয় তবুও তাকে মহান বলব?
তিনি অন্ধ দেশপ্রেমিক হতে নারাজ ছিলেন।
৫
দেশের প্রগতিশীল মানুষজন, এলাকার হিন্দু জনগোষ্ঠী যখন রামু সহিংসতা নিয়ে আহা-উহু করছে, মুক্তিযোদ্ধা কাকা বললেন, “তোমরা ইতিহাস ভুলে গেছো, আমরা এমন সমাজই বানিয়েছি, স্বাধীন দেশে যখন হিন্দুদের উপর অত্যাচার শুরু হলো, তখন তার বিরুদ্ধে কঠোর হস্তক্ষেপ হয়নি। তখনও আওয়ামী শাসন ছিল, এখনও তাই। সেদিন নতুন দেশে আমাদের সুযোগ ছিল সমাজটাকে একটা আদল দেয়ার। তিল তিল করে গড়ে তোলার।“
এটা আমার কাছে খুব ইন্টারেষ্টিং লাগতো যে, কাকা কখনো সংবিধানের সেক্যুলারিজম এর কথা বলতেন না। তিনি যখন বলছেন সমাজকে আদল দেয়ার /সমাজের মান নির্ধারণের কথা তখন তিনি সমাজের সমষ্টিগত রূপ/চরিত্র নিয়ে কথা বলছেন। তাঁর চিন্তায় সাম্প্রদায়িকতা মোকাবেলায় রাষ্ট্রের সংবিধান থেকে সমাজকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।[1] তিনি মনে করতেন, ১৯৭২-এ নবগঠিত সরকার সেকুলার সংবিধানের পাশাপাশি একটা সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তোলার কথা ভাবতো তাহলে হয়তো আজকে এমন সাম্প্রদায়িক সহিংসতার মুখোমুখি হতে হতো না।
তার একটা খুব প্রিয় বচন ছিল, যেমন ফলের চারা গাছ লাগাবে, সেই ফলই ধরবে গাছে। আম গাছে কাঠালতো ধরবে না।[2]
মুক্তিযোদ্ধা কাকার প্রিয় বচন দিয়েই লেখাটা শেষ করলাম। তাঁর এই কটাক্ষ ’১৯৭৫-পূর্ব বাংলাদেশকে বিশ্লেষনের কেন্দ্রে নিয়ে আসে; স্বাধীন রাষ্ট্রের ফরমেটিভ পিরিয়ড হিসেবে উপ্সথাপন করে। সচরাচর এই সময়কালটা যুদ্ধের ক্ষয় ক্ষতি, ৭৪’ দুর্ভিক্ষ ও জাতির জনকের নির্মম হত্যার ঘটনা দ্বারা বিশেষায়িত, আলাপ-আলোচনা প্রধানত তাতেই ঘুরপাক খায় । কিন্তু ১৯৭২-এর অরাজকতা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি যখন প্রশ্ন করেন, “দেশটাকে গড়ে তোলার সংগ্রামে কেউ শামিল হল না কেন? দু’দিন আগেইতো এই দেশের মানুষ দেশের জন্য মরতে প্রস্তুত ছিল?” তাঁর এই প্রশ্ন সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রে আওয়ামী সরকার ও তৎকালীন সমাজকে ভিন্নভাবে কাঠগড়ায় দাঁড় করায়। স্বাধীনতা ও দেশপ্রেমবোধের আপেক্ষিকতা নিয়ে মনে জিজ্ঞাসা তৈরি হয়।
বাংলাদেশের জন্মলগ্নে বিবাদমান সামাজিক বিভেদগুলোকে ভাঙ্গার হয়তো সুযোগ ছিল। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা কাকার হিসেবে ঔপনিবেশিক শাসনামল ছিল না। গাছের চারাতো সেই কলোনিকালেই লাগানো হয়েছে, সাম্প্রদায়িকতার বিষ/বীজ আরও আগেই বপন করা হয়েছে। তবে তাঁর এই তীর্যক মন্তব্যে একটা প্রশ্ন আমি কিছুতেই মাথাটা থেকে হটাতে পারিনি – রাষ্ট্র, সরকার ও সমাজের মধ্যে যে পরস্পরের পরিপূরক সম্পর্ক কল্পনা করা হয়, বাস্তবে কি আদৌ তাই? ধরুন, একটি নারী সংগঠনের এই শ্লোগানটির কথা – রাষ্ট্র হবে ইহজাগতিক, সমাজ হবে সাম্যবাদী, ব্যাক্তি হবে অসাম্প্রদায়িক। এখানেও সেই পরিপূরক সম্পর্ক কল্পনা করা হয়েছে, কিন্তু আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তির যে অন্তর্গত সংঘাত আছে সে বিষয়টির মীমাংসা কি করে হবে? বা আদৌ কি এটা মীমাংসাযোগ্য?
আম গাছে কাঁঠাল ফলের আলাপ থেকে অনেক দূরে সরে আসলাম।
তবে নৃবিজ্ঞানের ছাত্রী হিসেবে, বিশেষ করে সাবল্টার্ন স্টাডিজের তত্ত্ব ও পদ্ধতি দ্বারা অনুপ্রাণিত একজন শিক্ষার্থী হিসেবে একটি প্রসঙ্গ না পাড়লেই নয়। বিষয়টি মুক্তিযোদ্ধা কাকার ইতিহাস চর্চা নিয়ে। তিনি স্থানীয় পত্র–পত্রিকা পড়ে এবং নিজের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে ইতিহাসের এক অলিখিত বয়ান তৈরি করেছিলেন, যে বয়ান তাঁর কমুউনিটির মানুষকে বাংলাদেশ বুঝতে সাহায্য করেছে। পশ্চিমা বিদ্যাজগতে প্রতিষ্ঠিত সাবল্টার্ন হিস্টোরিয়ানরা যে মুদ্রিত ইতিহাস লেখেন তাঁর থেকে মুক্তিযোদ্ধা কাকার ইতিহাস চর্চার লক্ষ্য, পদ্ধতি এবং (অমুদ্রিত) প্রকাশ ভিন্ন। সাবল্টার্ন হিস্টোরিয়ানদের এযাবৎ কাজকে বিবেচনায় নিলে, এ কথা বলা ভুল হবে না যে মুক্তিযোদ্ধা কাকার মতন ব্যক্তিত্ব তাঁদের কাজে অলিখিত স্থানিক ইতিহাসের কণ্ঠমাত্র। আমি মনে করি তাঁর কণ্ঠ অলিখিত হলেও, অশ্রুত ছিল না। জ্ঞান জগতের রাজনীতি ও চর্চিত অসমতার কথা মাথায় রেখে তাই আমার প্রশ্ন, ক্যান দ্য সাবল্টার্ন বি এ হিস্টোরিয়ান?
১. রাষ্ট্র, সমাজ ও সংবিধানের এই কন্সেপচুয়াল পার্থক্য খুব জরুরি, কিন্তু আবার কোথায় এবং কখন এই বিভাজনগুলো মলিন বা অদৃশ্য হয়ে যায় সেটাও ভাববার ব্যাপার। আমি কাকার সাথে এই পর্যন্ত একমত যে আমাদের আলোচনা সংবিধানের অসাম্প্রদায়িক চেতনাকেন্দ্রিক হওয়ার কারণে রাষ্ট্র ও সমাজের সম্পর্কটা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সচারচর বাদ পড়ে যায়। কেন সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার বিধান থাকলেও সমাজ-রাষ্ট্র-সরকার তার থেকে পিছলে যায়? হিন্দু প্রতিবেশীর রোদে মেলে দেয়া হলুদে বালু মেশানোর উসকানিটা, সামাজিক মদতটা কোথা থেকে আসে? সরকার কেন নিয়ম উপেক্ষা করে বারে বারে হিন্দু পরিবারের জমি অধিগ্রহণে উদ্যত হয়?
২. এটা সত্য যে আমাদের দেশে একটা প্রবণতা আছে, বিশেষ করে আওয়ামীঘেষা প্রগতিশীল মহলে ১৯৭১ পরবর্তী শাসনামলটিকে বিশ্লেষণের বাইরে রেখে ইতিহাসের হিসেবে-নিকেশ করে।
লেখাটির পিডিএফ কপি ডাউনলোড করুন: muktijodha-kaka-can-the-subaltern-be-a-historian-saydia-gulrukh

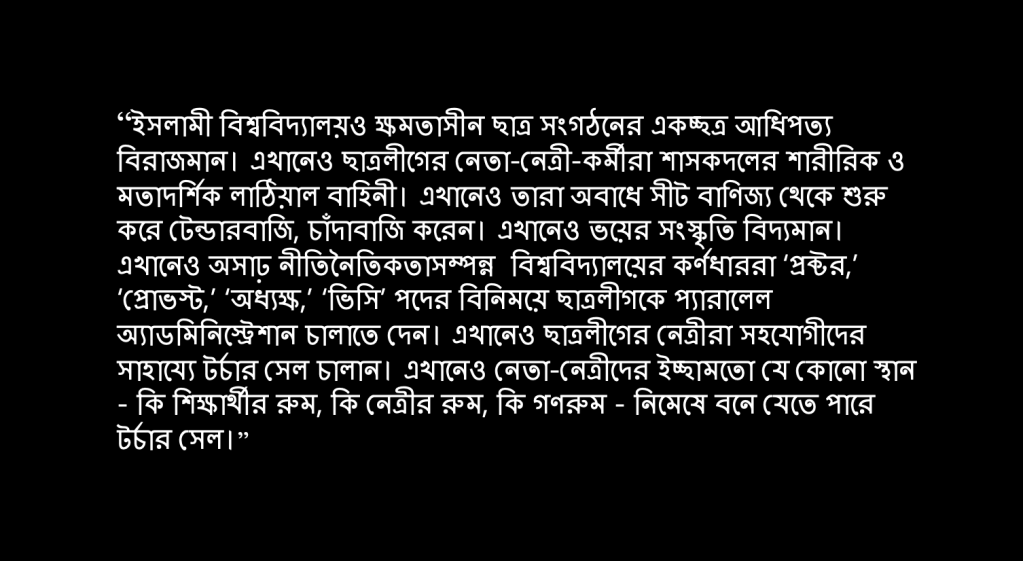


Leave a comment