নাসরিন খন্দকার
যৌন সহিংসতার সাথে যৌনসম্পর্কের কোনো সম্বন্ধ নাই। সহিংসতা মানে ক্ষতি করা, সীমা লংঘন করা, হেনস্তা করা, অন্য মানুষকে নাজেহাল করা। যৌন সহিংসতা একটা ক্ষমতাসম্পর্কের বিষয়, যৌনসম্পর্কের বিষয় নয়। ‘যৌন’ পদটা এখানে ব্যবহার করা হয় সহিংসতার মাধ্যম বোঝাতে, সহিংসতার উদ্দেশ্য বোঝাতে নয়। যৌন সহিংসতার লক্ষ্য সহিংসভাবে ‘যৌনকাজ’ করা নয়। বরং এটা যৌন যন্ত্রপাতি দিয়ে হিংস্রতা করা। আগ্রাসীর অন্তর্গত উদ্দেশ্য এখানে ক্ষতিসাধন করা, আঘাত দেয়া, অন্যকে নাজেহাল করা, যৌনকাজ করা নয়। আমরা কেন তাহলে ঠিক উল্টাভাবে চিন্তা করতে থাকি? কেন আমরা মনে করি যে অপরাধীর লক্ষ্য ছিল একটু যৌনকাজ করা, যা পূরণ করতে গিয়ে কিনা পরিশেষে আগ্রাসী হতে হয়েছে? এরকম মনে করার কারণ হতে পারে আমরা বিশ্বাসই করি যে যৌন কাজকর্মের মধ্যে আগ্রাসন অন্তর্ভুক্ত থাকাটা সম্ভব।
যৌনসম্পর্ক নিয়ে আমাদের এই ধারণাটি একটি ঐতিহাসিকভাবে গঠিত ধারণা যা নারীর প্রতি বৈষম্যের কেন্দ্রীয় দিক। নারী-পুরুষের বিষমকামী যৌনতার ধারণাতে মনেই করা হয় পুরুষ এখানে কর্তা এবং নারী অক্রিয়। মনে করা হয় নারীসত্তা তাঁর শরীরে সীমিত, যে শরীর পুরুষের যৌন আনন্দ এবং তাঁর সন্তানজন্মদানের আধার বা বস্তু। যৌনতার এই সামাজিক ব্যবস্থাপনায় নারীর শরীর পুরনরুৎপাদনের উপায় বা কারখানা হিসেবে মনে করা হয়, নারীকে সক্রিয় সত্তা হিসেবে বিবেচিত করা হয়না। এই পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায়, নারীর যৌন আনন্দ, যা কিনা পুনরুৎপাদন কেন্দ্রিক যৌনতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে, তা সম্পূর্ণভাবে বাদ পরে যায়, যাকে গায়ত্রী স্পিভাক ভগাঙ্কুরের মতাদর্শিক-বস্তুগত দমন (ideologico-material repression of the clitoris) বলছেন (১৯৮১, পৃষ্ঠা ১৮৯)। অন্যদিকে যৌনতার এই ধারণায় পুরুষ শুধু সক্রিয় সত্তাই না, শুধুমাত্র পুরুষের অর্গাজমকেই যৌনতার একমাত্র বিবেচ্য মনে করা হয়। উপরন্তু সমাজের আকাঙ্খিত পুরুষ হয়ে উঠার মাধ্যমে তাকে হয়ে উঠতে হয় আগ্রাসী পুরুষ, ফলে পুরুষের আগ্রাসী যৌনতা আর যৌনআনন্দকেই ‘স্বাভাবিক যৌনসম্পর্ক’ ধরে নেয়া হয় এবং তার পুনরুৎপাদন চলতে থাকে। ফলে আমরা যখন মনে করি যে যৌনসম্পর্কের মধ্যে আগ্রাসন এবং সহিংসতা থাকা ‘স্বাভাবিক’, তখন আমরা আসলে যৌনতার এই বৈষম্যমূলক ধারণাকেই প্রতিফলিত করি, যে ধারণা থেকেই ধর্ষণ সংস্কৃতির জন্ম।
কিন্তু যখন আমি বলছি যে যৌন সহিংসতা যৌনসম্পর্কের বিষয় নয়, তখন আমি ‘সম্পর্কের’ উপরে জোড় দিচ্ছি এবং এমন একটি সম্পর্কের প্রস্তাবনা এবং চর্চার কথা বলছি যেখানে পুরুষ কর্তা এবং নারী অক্রিয় নয়, দুজনেই কর্তা এবং এটি একটি পারস্পরিক সম্পর্ক যার মাধ্যমে উভয়েরই যৌন তৃপ্তি ঘটে। এই ‘সম্পর্ক’ সম্ভবপর হয়ে উঠতে পারে পারস্পরিক আনন্দলাভের মধ্য দিয়ে। এই যৌনসম্পর্ক পুনরুৎপাদনের যৌনব্যবস্থাপনা থেকে আলাদা। ফলে যৌনসম্পর্কের এই কল্পনা সমাজে বিদ্যমান পিতৃতান্ত্রিক এবং লিঙ্গবাদী যৌনতার ধারণাকে ভেঙ্গে দিয়ে সমতাভিত্তিক যৌনসম্পর্কের কল্পনা থেকে আসে।
সমতাভিত্তিক যৌনসম্পর্কের এই কল্পনা এবং চর্চা ধর্ষণ মোকাবেলায় মৌলিক হলেও বাস্তবতায় এর পথ অনেক দীর্ঘ। আমার নিজের জন্যে বাংলাদেশে একজন নারী হিসেবে বেড়ে উঠার অন্যতম সামাজিক শিক্ষা ছিল যৌনতা থেকে নিজকে রক্ষা করে চলা। বড় হতে হতে আমি শিখেছি যৌনতা পুরুষের বিষয়। পুরুষ নারীর কাছ থেকে যৌনতা এবং যৌন আনন্দ চায় এবং আমার নিজেকে পুরুষের এই কামনা থেকে বাঁচিয়ে চলতে হবে। পরবর্তীতে পুরুষের যৌন আগ্রহ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলার প্রবণতা আমার নারীবাদী চেতনা বিকাশের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে আমাকে ধর্ষণ এবং যৌন নিপীড়ন বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত করে। কিন্তু যৌনসম্পর্ক থেকে যৌন-সহিংসতাকে আলাদা করে বুঝে নিতে আমার আরও অনেক বছর লেগে যায়। এমনকি ধর্ষণের বিপরীতে যে আসলে রয়েছে নারীর মানুষ হিসেবে নিজের শরীর এবং যৌনতাকে উপভোগ করার অতি মৌলিক মানবাধিকার, সেইটা বুঝতে আমার যুগ পার হয়ে যায়। এত দেরী হবার কারণ হোল, এমনকি নারীবাদী মহলেও যৌন রাজনীতি যা নারীকে যৌন বস্তুতে সীমিত করে, তাকে ধর্ষণের প্রতিরোধে কেন্দ্রে রাখা হয়না। দুঃখজনক যে নারী এবং প্রান্তিক লিঙ্গের যৌন কর্তাসত্তার বিষয়টি এতটাই ‘নিষিদ্ধ’ যে এর প্রতি গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমেই যে ধর্ষণ সংস্কৃতি রোধ সম্ভব তা আলোচনায় আসে না।
আমরা যখন ধর্ষণ-বিরোধী প্রতিবাদ করি তখন আমরা মূলত এমন একটি ঘটনার প্রতিরোধ করি যার মাধ্যমে একজন ধর্ষক ধর্ষণের শিকারকে লঙ্ঘিত করে একধরনের আনন্দ লাভ করে। ধর্ষণের শিকার হয় যে ব্যক্তি, ধর্ষণের ফলে তাঁর নিজ শরীরের মালিকানা এবং তা উপভোগ করার অধিকার লঙ্ঘিত হয়। উপরন্তু এর মাধ্যমে ধর্ষণের শিকার আহত হন, তার শরীর লঙ্ঘিত এবং নিপীড়িত হয়। এটি তাই যৌনসম্পর্ক হতেই পারেনা, এটি ধর্ষণ। ফলে এটি শুধুমাত্র শারীরিক ক্ষতি বা আঘাতই নয়, এটি মানুষ হিসেবে নিজের শরীর এবং যৌনতা উপভোগ করার মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন। কিন্তু মুশকিল হোল ধর্ষণের সংস্কৃতিতে নারীর যৌনসত্তাকে যেভাবে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দেয়া হয়, তা এত ব্যপক এবং যৌন-সহিংসতার বাস্তবতা এতটাই তীব্র যে নারীবাদী প্রতিরোধ শুধুমাত্র লঙ্ঘিত না হবার মধ্যেই সীমিত রয়ে যায়। এটি লিঙ্গবাদের সহিংসতা এবং প্রান্তিক লিঙ্গের যৌন কর্তাসত্তার প্রসঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারেনা।
উপরন্তু আমরা দেখি যে ধর্ষণের বিচার পাবার জন্যে ধর্ষিতা যে ‘নিষ্পাপ’ তা তাঁর অযৌন সত্তা বা অক্রিয়তা দিয়ে প্রমাণ করা জরুরী হয়ে পরে। অর্থাৎ ধরেই নেয়া হয়, নিষ্পাপ হবার পূর্বশর্ত হোল যৌনতা বিসর্জন। এই ধরনের চিন্তাকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় তা কতটা অবান্তর। এই ধারণা অনুসারে যৌনতাকে মনে করা হয় আগ্রাসী, পুরুষালি এবং পাপ এর ধারণার সাথে যুক্ত। এরকম চিন্তা যৌন রাজনীতির দ্বারা সৃষ্ট যা নারীকে বস্তু এবং পুরুষকে কর্তা হিসেবে বিপরীতে রাখে। এই চিন্তা ভিক্টোরীয়, উপনিবেশিক এবং ব্যাক্তিবাদি পুঁজিবাদ যা শুধুমাত্র হেজেমনিক পৌরুষের ধারণাকে ব্যাক্তির বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, তার ইতিহাসে গ্রথিত। এই বয়ানে মনে করা হয় যৌনতায় নারীর ভূমিকা হচ্ছে পুরুষের ইচ্ছায় ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ বলে প্রতিক্রিয়া জানানো। ফলে নারী এখানে কখনই যৌনকর্মের কর্তা না, যদি কখনও সে হয়ও তাহলে তাকে চরিত্রহীন বা বেশ্যা মনে করা হয়। এই বয়ানের চক্র ভেঙ্গে দেবার জন্যে তাই দরকার ঐতিহাসিকভাবে যাদের কর্তাসত্তাকে হরণ করা হয়েছে যৌনবস্তুতে সীমিত করে তোলার মাধ্যমে তাঁদের সেই সত্তাকে দাবী করা।
ধর্ষণের প্রতিরোধে আমরা সম্মতির ধারণাকে কেন্দ্রীয় গুরুত্ব দেই। এটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু নারীর যৌন কর্তাসত্তার জন্যে আমাদের আসলে আরও বেশী কিছু দরকার। সম্মতির এই বয়ান পুরুষের ইচ্ছার প্রতি নারীর উত্তর দেবার অধিকারকে কেন্দ্রে রাখে। ধরে নেয়া হয় পুরুষ ইচ্ছা প্রকাশ করবে এবং নারী সেই ইচ্ছায় প্রতিক্রিয়া জানাবে। এই বয়ানে যৌনক্রিয়ায় নারীর দ্বিতীয় বা গৌণ ভূমিকা ধরে নেয়া হয়। উপরন্তু শুধুমাত্র ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ দিয়ে সংজ্ঞায়িত করাটাও সমস্যাজনকভাবে সম্মতিকে সীমিত করে। ‘না’ মানে যে ‘আমাকে হ্যাঁ বলাও’ বা ‘হয়ত পরে হ্যাঁ বলব চেষ্টা করা যাও’ না, তা স্পষ্ট করা জরুরী। তেমনি এটা মনে রাখা দরকার যে ‘হ্যাঁ’ মানে সবসময়ই যে ‘হ্যাঁ’ তা না। ‘হ্যাঁ’ শর্তসাপেক্ষিক হতে পারে। এমনকি জোর করেও ‘হ্যাঁ’ আদায় করা হতে পারে। ফলে শুধুমাত্র ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ বলা দিয়ে সম্মতিকে বুঝতে যাওয়া যথেষ্ট না। যখন ধর্ষণ-বিরোধী আন্দোলনকারীরা জোর দেন যে ‘না’ মানে ‘না’ এবং শুধুমাত্র ‘হ্যাঁ’ মানেই ‘হ্যাঁ’, তখন যৌনতার ঐ ঐতিহাসিক নির্মাণকে বিবেচনা করেনা যা যৌনকর্মে পুরুষের ইচ্ছা প্রকাশের উত্তরে নারীকে অক্রিয় এবং বিশেষ রকম ভূমিকা পালনে পরিচালিত করে। সব ‘হ্যাঁ’ যে সত্যিকার ইচ্ছাপ্রকাশ নাও হতে পারে তা দেখতে দেয়না। সত্যিকারের ইচ্ছাপ্রকাশ করবার জন্যে প্রয়োজন পরে একটি বিশেষ সামাজিক অবস্থা যেখানে নারীর যৌন আনন্দ উপভোগ করা সম্ভবপর। যেখানে নারীর অর্গাজম, এবং তাঁর কর্তাসত্তা সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারে। ফলে ধর্ষণ প্রতিরোধের জন্যে প্রয়োজন এরকম সামাজিক বাস্তবতার নিশ্চয়তা যেখানে নারীর অর্গাজম, যৌন কর্তাসত্তার প্রশ্ন আলোচিত হতে পারবে, এবং সম্মানহানি না করেই নারী এবং সকল প্রান্তিক লিঙ্গের ব্যক্তির কামনার স্বীকৃতি এবং অধিকার মিলবে।
সম্মতির আলোচনাকেও শুধুমাত্র যোগাযোগের বিষয় না, বরং নৈতিকতার বিষয় হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এখানে আমি নৈতিকতা বলতে পুরুষতান্ত্রিক নৈতিকতার ধারণা যা যৌনতাকে নারীর জন্যে ক্ষতিকর এবং সম্মানহানিকর মনে করা তার কথা বলছিনা, বরং উল্টোটা বলছি । এখানে নৈতিকতা বলতে বোঝাচ্ছি এমন নীতি বা আচরণ যা একজনকে অপর ব্যক্তির ক্ষতি করা থেকে বিরত রাখবে। এখানে যৌনসম্পর্কে অংশ নেয়া দুজনেরই পরস্পরের প্রতি নৈতিক আচরণ করা জরুরী। সম্মতি আর নৈতিক আচরণ দুইটা ভিন্ন বিষয়। নৈতিক আচরণ সম্মতির চেয়ে বেশী কিছু। ধর্ষণ মোকাবেলায় সম্মতি অতীব জরুরী, কিন্তু ধর্ষণের সংস্কৃতি মোকাবেলায় আমাদের দরকার আরও বেশী কিছু, দরকার সম্মতি এবং যৌনসম্পর্কে পরস্পরের প্রতি নৈতিক আচরণ।
ধর্ষণ সংস্কৃতির একটি অন্যতম মৌলিক ভিত্তি হচ্ছে নারী এবং তাঁর শরীরকে যৌন বস্তু হিসেবে বিবেচনা করা। এই ধরণের লিঙ্গবাদ ভোগবাদী পুঁজিবাদের সহকারী হিসেবে কাজ করে। এই কাঠামোগত বাস্তবতায় বাস করে আমরা নিজেরাও আমাদের মধ্যে এই লিঙ্গবাদকে কমবেশি ধারণ করি। আমাদের শরীরকে যৌনবস্তুতে সীমিত করার এই প্রক্রিয়া সহজেই দুর করা সম্ভব না। কিন্তু আমরা আমাদের নিজের যৌন কর্তাসত্তা দাবী করার মাধ্যমে এই প্রক্রিয়াকে দুর্বল করে তুলতে পারি। আমরা সেই নারী হয়ে উঠতে পারি যারা সম্মানের সাথে নিজেদের কামনা এবং যৌনতা উপভোগ করতে পারে। আমরা সেই নারী হয়ে উঠতে পারি যার শুধু সম্মতি প্রদানের অধিকারই না, সেই সাথে যৌন ইচ্ছা প্রকাশ করার অধিকারও রয়েছে। নিজদের যৌন কর্তাসত্তা দাপট এবং সম্মানের সাথে দাবী করতে পারলেই প্রতিদিনকার লিঙ্গবাদ এবং ধর্ষণের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিজয় অর্জন করতে পারব।
নাসরিন খন্দকার একজন মা, নারীবাদী এবং নৃবিজ্ঞানী যিনি ভয়াবহ দুর্যোগেও আশা রাখার মতো বোকামি করতে থাকেন।


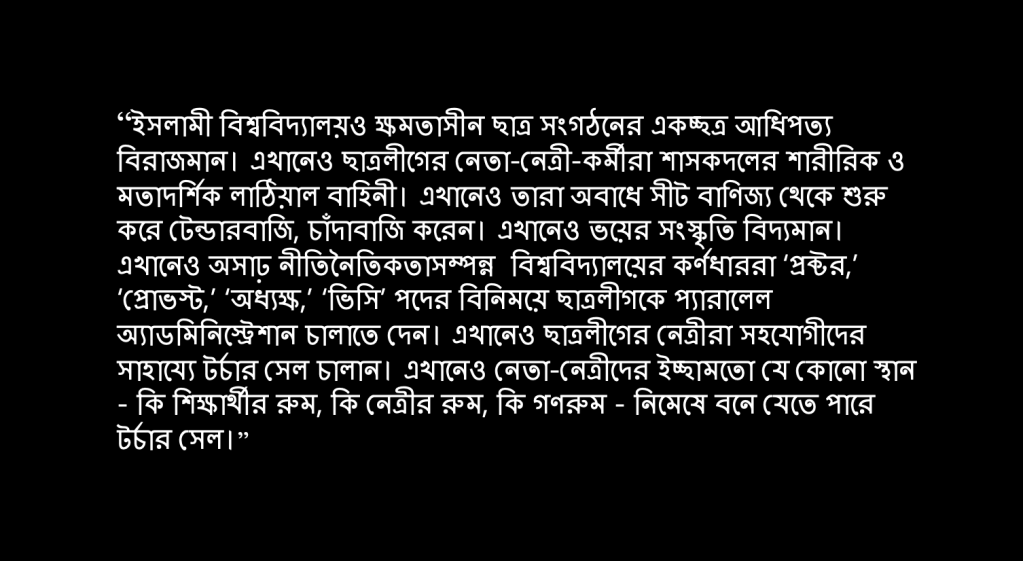


Leave a comment